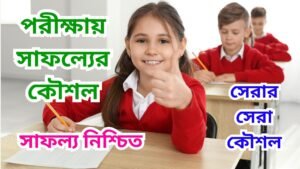নরমপন্থী বা আদি কংগ্রেসের কার্যাবলী বা কর্মসূচী, সাংবিধানিক সংস্কার হিসেবে রাজকীয় কমিশন গঠন, ভারত সচিবের পরিষদ বিলোপ, মন্ত্রণা পরিষদে ভারতীয় সদস্য গ্ৰহণ, স্বায়ত্তশাসন অর্জন, অর্থনৈতিক সংস্কার হিসেবে শিল্প সংক্রান্ত দাবি, কৃষি সংক্রান্ত দাবি, ব্যয় সংকোচের দাবি, শাসনতান্ত্রিক সংস্কার হিসেবে প্রশাসনের ভারতীয়করণ, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে দাবি, জনসেবামূলক দাবি, নাগরিক অধিকার রক্ষা, সরকারের সমালোচনা, আদি কংগ্রেসের কার্যাবলীর ত্রুটি এবং কৃষক ও শ্রেণী স্বার্থ সম্পর্কে জানবো।
নরমপন্থী বা আদি কংগ্রেসের কর্মসূচি বা কার্যাবলি সম্পর্কে কর্মসূচি ও দাবি গুলির সীমাবদ্ধতা, নরমপন্থী কংগ্রেসের কর্মসূচির ত্রুটি, আবেদন নিবেদন নীতি, নরমপন্থী কংগ্রেসের সাংবিধানিক সংস্কার কর্মসূচি, নরমপন্থী কংগ্রেসের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি, নরমপন্থী কংগ্রেসের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কর্মসূচি, নরমপন্থী কংগ্রেস কর্তৃক সরকারের সমালোচনা, নরমপন্থী কংগ্রেস ও শ্রেনীস্বার্থ সম্পর্কে জানব।
নরমপন্থী বা আদি কংগ্রেসের কার্যাবলী বা কর্মসূচী
| ঐতিহাসিক ঘটনা | নরমপন্থী বা আদি কংগ্রেসের কার্যাবলী |
| সময়কাল | ১৮৮৫-১৯০৫ |
| নেতৃবৃন্দের পরিচিতি | নরমপন্থী |
| কর্মপন্থা | আবেদন-নিবেদন |
| লক্ষ্য | কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ |
ভূমিকা :- ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ নরমপন্থী বা মডারেট নামে পরিচিত।
নরমপন্থী কংগ্রেসের কর্মসূচি
এই যুগে কংগ্রেসের পক্ষে যে-সব দাবি-দাওয়া উত্থাপিত হয় তা চারভাগে বিভক্ত করা যায়-
- (ক) সাংবিধানিক সংস্কার,
- (খ) অর্থনৈতিক সংস্কার,
- (গ) শাসনতান্ত্রিক সংস্কার এবং
- (ঘ) নাগরিক অধিকার রক্ষা।
(ক) সাংবিধানিক সংস্কার
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার দাবি করেন নি—তাঁরা বিভিন্ন অধিবেশনে বেশ কিছু সাংবিধানিক সংস্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাঁরা ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের অধিক ক্ষমতা দান, ব্যবস্থাপক সভা বা আইন পরিষদগুলিতে অধিক সংখ্যক নির্বাচিত ভারতীয় সদস্য গ্রহণ এবং এগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধির দাবি করেন।
(১) রাজকীয় কমিশন গঠন
উপযুক্ত সংখ্যক ভারতীয় সদস্য নিয়ে একটি ‘রাজকীয় কমিশন’ (‘Royal Commission) গঠন করে ভারতীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান দাবি করা হয়।
(২) ভারত সচিবের পরিষদের বিলোপ সাধন
‘ইন্ডিয়া কাউন্সিল’ (‘India Council) নামক ভারত সচিবের মন্ত্রণা পরিষদের অবসানের দাবি করা হয়।
(৩) নিখিল ভারতীয় ও প্রাদেশিক সভার সংস্কার
সমানুপাতিক হারে নির্বাচিত সদস্য নিয়ে নিখিল ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সংস্কার এবং সদস্য সংখ্যা ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরা।
(৪) অযোধ্যা,পাঞ্জাবে ব্যবস্থাপক সভা গঠন
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, অযোধ্যা ও পাঞ্জাবে অনুরূপ ব্যবস্থাপক সভা গঠনকরা।
(৫) ভারতীয় সদস্য গ্ৰহণের দাবি
নিখিল ভারতীয় শাসন পরিষদে অন্ততপক্ষে দু’জন এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রাদেশিক শাসন পরিষদে একজন করে ভারতীয় সদস্য গ্রহণ প্রভৃতি দাবি জানায়।
(৬) ব্রিটিশ কমন্স সভায় ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণ
১৯০৪ সালে কংগ্রেস দাবি করে যে, ব্রিটিশ কমন্স সভায় প্রতি প্রদেশ থেকে অন্তত দু’জন করে প্রতিনিধি পাঠাতে হবে।
(৭) মন্ত্রণা পরিষদে ভারতীয় সদস্য
ভারত সচিবের মন্ত্রণা পরিষদে তিনজন ভারতীয় গ্রহণের দাবিও জানানো হয়। এই সব দাবি সরকারের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা সম্ভবহয় নি।
(৮) ভারত শাসন আইন ১৮৯২
কংগ্রেসের দাবি গুলি পেল করার পর সরকার ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ‘ভারত শাসন আইন’ প্রণয়নে বাধ্য হয়। এই আইনের মাধ্যমে ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয় নি এবং তাঁরা এই সব দাবিগুলি করতেই থাকেন।
(৯) স্বায়ত্তশাসন অর্জন
১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-এর অভ্যন্তরে স্বায়ত্তশাসন অর্জন করাই হল কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য।
(খ) অর্থনৈতিক সংস্কার
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং ভারতে আধুনিক শিল্প ও কৃষির অভাবের জন্য জাতীয় কংগ্রেস ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নীতিকেই দায়ী করে।
(১) নৌরোজির অভিমত
১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে দাদাভাই নওরোজি সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, “ব্রিটিশ শাসন একটি স্থায়ী এবং ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন-স্বরূপ। এই শাসন অতি ধীরে ধীরে ভারতকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।”
(২) শিল্প সংক্রান্ত দাবি
কংগ্রেস ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য দেশীয় শিল্পের বিকাশে উৎসাহ-দান এবং সেই সঙ্গে রক্ষামূলক শুল্ক আরোপ, সুতিবস্ত্রের ওপর থেকে বৈষম্যমূলক শুল্ক অপসারণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংরক্ষণ দাবি করে।
(৩) কৃষি সংক্রান্ত দাবি
কৃষির উন্নতি ও কৃষকের ওপর আর্থিক চাপ কমানোর জন্য জাতীয় কংগ্রেস জমির কর হ্রাস, জমির স্বত্ব আইনের পরিবর্তন, সমগ্র ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-এর প্রসার, রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত এলাকায় রাজস্ব হ্রাস ও রাজস্ব আদায়ের কঠোরতা হ্রাস, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, সমগ্র দেশে কৃষি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা, বন সংরক্ষণের দাবি জানায়।
(৪) বন আইনের সরলীকরণ
আদিবাসীদের সুবিধার জন্য বন আইনের সরলীকরণ ও বাধ্যতামূলক শ্রমের বিলোপ সাধন করার দাবি জানায়।
(৫) ব্যয় সংকোচের দাবি
‘হোমচার্জ’ (Home) Charges) বাবদ বিভিন্ন খাতে ভারত থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংল্যান্ড প্রেরিত হত তার পরিমাণ হ্রাস করা, আয়কর ও লবণ করের বোঝা কমানো, আবগারি শুল্কের বিলোপ এবং সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচের দাবি জানানো হয়।
(৬) বিপান চন্দ্রের অভিমত
ডঃ বিপান চন্দ্র বলেন যে, অর্থনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের এই ক্রমবর্ধমান প্রচারের ফলে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে দেশবাসীর মনে একটি ধারণা গড়ে ওঠে। তাদের মনে এ কথা গভীরভাবে বন্ধমূল হয়ে যায় যে, ব্রিটিশ শাসনের কিছু পরোক্ষ সুফলের চেয়ে প্রত্যক্ষ কুফল অনেক বেশি এবং ব্রিটিশের শোষণই ভারতের দারিদ্র ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূল কারণ।
(গ) শাসনতান্ত্রিক সংস্কার
শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ শাসনব্যবস্থার উচ্চ ও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে ভারতীয়দের নিয়োগের দাবি জানান।
(১) প্রশাসনের ভারতীয় করণ
তাঁরা মনে করতেন যে, প্রশাসনের ভারতীয়করণ’হলেই ভারতবাসীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত হবে। ইংরেজ কর্মচারীদের উচ্চ বেতন দানের ফলে ভারতের টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে। প্রশাসনের ভারতীয়করণ হলে দেশের টাকা দেশেই থাকবে এবং ভারতীয় কর্মচারীরা দেশের স্বার্থেই কাজ করবেন।
(২) গোখলের অভিমত
১৮৯১ সালে গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলছেন যে, “বিদেশি ইংরেজদের দিয়ে গঠিত শাসনব্যবস্থা শুধু ব্যয়বহুল রূপেই অশুভ নয়—নৈতিক দিক থেকেও এই ব্যবস্থা যথেষ্ট আপত্তিজনক ও হানিকর। এই ব্যবস্থা ভারতীয় জাতির মানসিক গঠনকে পঙ্গু করে দিচ্ছে।… আমাদের দেশের বহু মানুষের মধ্যে যে সামরিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা আছে তা অব্যবহারের ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।”
(৩) সরকারি চরকারির ক্ষেত্রে দাবি
চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেস একই সময়ে ভারত ও ইংল্যাণ্ডে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণ, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স উনিশ থেকে একুশ করা এবং ‘স্ট্যাটুটারিস্ট্যাটুটারি’ সিভিল সার্ভিসের অবসান প্রভৃতি দাবি করে।
(৪) প্রশাসনিক দাবি
শাসনবিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, জুরি ব্যবস্থার প্রবর্তন, পুলিশ-প্রশাসনে সংস্কার, ভারতীয়দের সামরিক শিক্ষা দান ও উচ্চ সামরিক পদে নিয়োগ এবং আত্মরক্ষার জন্য ভারতীয়দেরও অস্ত্র রাখার অধিকার দেবার দাবি জানানো হয়।
(৪) জনসেবামূলক দাবি
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, জনসেবামূলক কর্মধারা গ্রহণ করাও সরকারের অবশ্য কর্তব্য। এই কারণে তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, কারিগরি ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, জনস্বাস্থ্য ও সুচিকিৎসার দাবি জানিয়েছিল।
(৫) গান্ধীর আন্দোলন সমর্থন
দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়, মরিশাস, ফিজি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ব্রিটিশ গায়েনা প্রভৃতি স্থানে কর্মরত ভারতীয় শ্রমিকদের চরম বর্ণবিদ্বেষ ও নানা অনাচারের শিকারে পরিণত হয়ে দাসের মতো জীবন ধারণ করতে হত। এই অনাচারের বিরুদ্ধে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবল গণ আন্দোলন গড়ে তুললে জাতীয় কংগ্রেস তা অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করে।
(৬) শ্রমিকদের প্রতি সজাগ
বিদেশি মালিকানাধীন চা ও কফি বাগানে নামমাত্র মজুরিতে ও প্রবল অনাচারের মধ্যে কর্মরত ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সজাগ দৃষ্টি ছিল।
(গ) নাগরিক অধিকার রক্ষা
ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার রক্ষায় প্রথম পর্বের কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন দাবি পেশ করেন।যেমন –
(১) বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবি
নেতৃবৃন্দ ভারতবাসীর গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। এই কারণে বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে কংগ্রেস দাবি পেশ করে।
(২) কংগ্রেসের প্রতিবাদ
১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে সরকারি ফৌজদারি আইনকে কঠোরতর করা হয় এবং ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য সরকার গোপন কমিটি গঠন করলে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিবাদ জানায়।
(৩) সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাল গঙ্গাধর তিলক ও নাটু ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহমূলক রচনার অভিযোগ এনে তাঁদের শাস্তি প্রদান করলে জাতীয় কংগ্রেস তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে।
(৪) মুক্তি সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ
এরপর বাক্-স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য পুলিশের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হলে দেশময় প্রতিবাদ ওঠে। এইভাবে নাগরিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম দেশের মুক্তি সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।
নরমপন্থী কংগ্রেস কর্তৃক সরকারের সমালোচনা
- (১) ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি, অবাধ শোষণ, নিষ্ঠুর দমননীতি, সাধারণ মানুষের প্রতি প্রশাসনের দুর্ব্যবহার প্রভৃতির বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদে মুখর ছিলেন।
- (২) ইউরোপীয় শিল্পপতিদের স্বার্থে পরিচালিত দুর্নীতিগ্রস্ত ও স্বৈরাচারী শাসন ও বিচারব্যবস্থা, সরকারি চাকরিতে ভারতীয়দের প্রতি তীব্র বঞ্চনা, আদালতে ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও ভারতে জনহিতকর কার্যাবলী—অর্থাৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসালয় নির্মাণ প্রভৃতির প্রতি সরকারের ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেস সমালোচনায় সোচ্চার হয়।
- (৩) ভারতের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে সরকারের আগ্রাসী নীতি, বার্মা জয়, আফগানিস্তান আক্রমণ ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে আদিবাসীদের দমন প্রভৃতি কাজেরও সমালোচনা করা হয়।
- (৪) সরকারের স্বৈরাচারী, স্বার্থান্বেষী ঔপনিবেশিক ও অর্থনৈতিক নীতির বিভিন্ন দিক ও তার শোচনীয় ফলাফল দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে ভারতের শোচনীয় অর্থনৈতিক দুর্দশা ও দারিদ্রের জন্য ব্রিটিশ শাসনকে দায়ী করা হয়।
- (৫)ইংল্যাণ্ডের ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভারতে ইংরেজ শাসকদের আচরণে হতাশ ও মর্মাহত হন। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, শোষণ, স্বৈরাচার ও দমন-পীড়নই হল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি।
- (৬) বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা দাদাভাই নৌরোজি তাঁর বিখ্যাত ‘Poverty and Un-British Rule in India’ গ্রন্থে ভারতের দারিদ্রের জন্য ব্রিটিশ শাসনকে দায়ী করে ভারতে প্রচলিত শাসনব্যবস্থাকে “ব্রিটিশ ঐতিহ্য-বিরোধী’ (‘Un-British’) বলে আখ্যায়িত করেন।
- (৭) রমেশচন্দ্র দত্ত, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রমুখ নেতৃবৃন্দও ‘ব্রিটিশ ঐতিহ্য-বিরোধী’ এই শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন।
নরমপন্থী কংগ্রেসের কর্মসূচির ত্রুটি
বলা বাহুল্য, জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচি বা কর্মধারা একেবারে ত্রুটিহীন ছিল না।যেমন –
- (১) কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সাধারণ মানুষ বা স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার দাবি করেন নি।তাহার লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশের অধীনে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন—পূর্ণস্বাধীনতা নয়। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের কোনও অধিবেশনে ‘স্বরাজ’-এর দাবি নিয়ে কোনও প্রস্তাব গৃহীত হয় নি।
- (২) বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখেরা কংগ্রেস মঞ্চ থেকে এই দাবি উত্থাপন করার চেষ্টা করলে প্রাচীনপন্থী নেতৃবৃন্দ ‘চরমপন্থী’ বলে তাঁদের ভর্ৎসনা করেন। অন্যদিকে তরুণ নেতৃবৃন্দ প্রাচীন পন্থীদের ‘নরমপন্থী’ বলে বিদ্রুপ করতে থাকেন। এইভাবে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ‘নরমপন্থী’ ও ‘চরমপন্থী’ গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়।
- (৩) কৃষক ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের উন্নতির জন্য তাঁদের কোনও আকর্ষণীয় কর্মসূচি ছিল না। কৃষকদের দুর্গতি মোচনের জন্য কোনও আলোচনাও অন্তত ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোনও কংগ্রেস অধিবেশনে করা হয় নি।
- (৪) কৃষকদের জন্য সামান্য চিন্তা-ভাবনা করা হলেও, শ্রমিকদের জন্য সেটুকুও হয় নি। ঊনিশ শতকের শেষ দিকে বোম্বাই অঞ্চলে বস্ত্রশিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময়, কাজের পরিবেশ ও মজুরি—সবই ছিল সুস্থ জীবন যাপনের পরিপন্থী। কংগ্রেস নেতৃত্ব এ ব্যাপারে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেন নি।
- (৫) ‘ভারত সভা‘-র নেতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি বহু চেষ্টা করেও আসামের চা-বাগানের কুলিদের ওপর অত্যাচারের সমস্যাটি কংগ্রেস কর্মসূচির মধ্যে নথিভুক্ত করাতে পারেন নি। ক্ষুব্ধ দ্বারকানাথ কংগ্রেসের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।
- (৬) ভারতের দুর্গতির জন্য তাঁরা সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ শাসনকে দায়ী করেন নি — তাঁরা কেবল ‘অ-ব্রিটিশ নীতি’ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিলেন। ভারতের দুর্গতির জন্য একমাত্র সম্পদের বহির্গমন বা ‘নির্গমন তত্ত্ব’ই নয়—দেশীয় জমিদার ও মিল মালিকরাও যথেষ্ট দায়ী ছিলেন। নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ এই বিষয়ে কিছু বলেন নি।
নরমপন্থী কংগ্রেস ও শ্রেনী স্বার্থ
- (১) অনেক সময় প্রথম যুগের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক ছিল না, তাঁদের সামাজিক ভিত্তি ছিল। সংকীর্ণ এবং তাঁরা তাঁদের শ্রেণী-স্বার্থেই জাতীয় কংগ্রেসকে পরিচালিত করেছিলেন।
- (২) এই প্রতিষ্ঠান মূলত মুষ্টিমেয় ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চবিত্ত শহুরে মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তাঁরা কেবলমাত্র নিজ শ্রেণী স্বার্থে এই সংগঠনকে ব্যবহার করেছিলেন—এই অভিযোগ যথার্থ নয়।
- (৩) ডঃ তারা চাঁদ বলেন যে, “কংগ্রেস মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগঠন হলেও, সর্বশ্রেণীর প্রয়োজনের দিকেই এর নজর ছিল। এ জন্যই জাতীয় কংগ্রেস ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি, অবাধ শোষণ, নিষ্ঠুর দমননীতি, সাধারণ মানুষের প্রতি প্রশাসনের দুর্ব্যবহার, ভারতীয় সম্পদের নির্গমন, সরকারি চাকরিতে ভারতীয়দের বঞ্চনা, আসামের চা-বাগান ও বহির্ভারতে ভারতীয় শ্রমিকদের ওপর জুলুম প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।
- (৪) শ্রেণী-স্বার্থ নয়, দেশের সাধারণ মানুষের সুবিধার্থেই জাতীয় কংগ্রেস লবণ কর ও আয়কর হ্রাস, ক্ষুদ্র শিল্পের সংরক্ষণ, সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ, কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন, প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষার বিস্তার, চিকিৎসালয় নির্মাণ প্রভৃতির দাবি জানায়। এই সব দাবি নিশ্চয়ই উচ্চবিত্তদের শ্রেণী-স্বার্থে নয়।
- (৫) ডঃ বিপান চন্দ্র বলেন-“শুধু নিজেদের স্বার্থসাধনই তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের নীতি ও কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁরা চেয়েছিলেন সকল শ্রেণীর মানুষের দাবিকে সমর্থন করতে, দেশের মিলিত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে।”
উপসংহার :- ডঃ সুমিত সরকারবলেন যে, “আদি যুগের কংগ্রেস কেবলমাত্র ইংরেজি-শিক্ষিত বৃত্তিজীবী গোষ্ঠী, জমিদার বা শিল্পপতিদের স্বার্থ নিয়েই ভাবত না।” এর ইঙ্গিত মেলে লবণ কর, বিদেশে ভারতীয় কুলিদের প্রতি আচরণ ও অরণ্য প্রশাসনের কারণে দুর্দশা বিষয়ে অজস্র প্রস্তাবে।
(FAQ) নরমপন্থী বা আদি কংগ্রেসের কার্যাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য?
মডারেট বা নরমপন্থী।
আবেদন নিবেদন।
দাদাভাই নৌরোজি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।